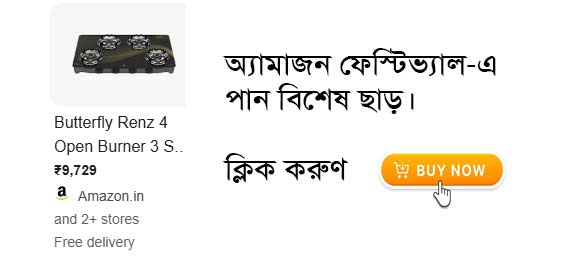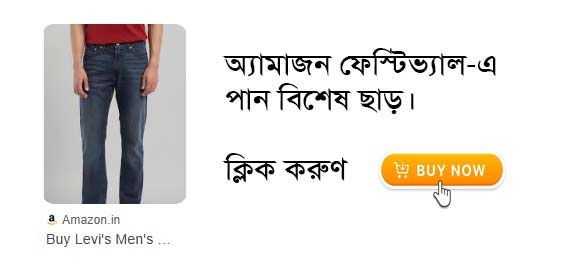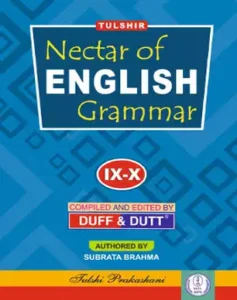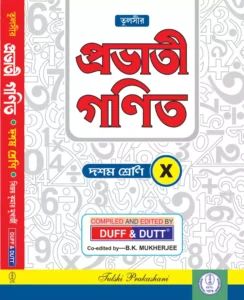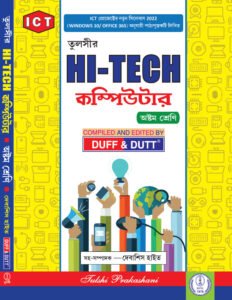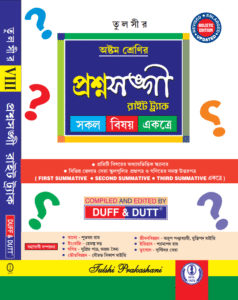সোমেন দত্ত, কোচবিহারঃ
শক্তির এক অনন্য রূপ তিনি। ভয়াল, রক্তপিপাসু। আবার মাতৃস্নেহময়ী। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, করালবদনা। সেই তিনিই শরণাগত সন্তানের জন্য আশ্রয়দাত্রী ও অভয়ময়ী। এত বিপরীত ছবি একসঙ্গে ধারণ করেছেন কি আর কোনও ঈশ্বর!
সনাতন ধর্মে কালী শুধু এক ঈশ্বরের নাম নয়, বরং গভীর দর্শনের দর্পণও। যেখানে মৃত্যু, সময়, ধ্বংস ও সৃষ্টি এক অভিন্ন শক্তিতে রূপ নেয়। আর সেই শক্তির পরিধি এতই বিস্তৃত, যে তার উপাসনা ঘরোয়া-সর্বজনীন হয়ে উঠতে সময় নেয়নি।
‘কাল’ শব্দটির অর্থ সময়, মৃত্যু, কিংবা কৃষ্ণবর্ণ। আবার এই ‘কাল’ শব্দই শিবের অন্যতম নাম। যিনি সময়ের ঊর্ধ্বে অনন্ত শাশ্বত চেতনার প্রতীক। তাঁর স্ত্রীরূপ কালী, যিনি কাল বা মৃত্যুর সংহারিণী। শাক্ত দর্শনে কালী শুধুই এক ভয়ঙ্করী নন, তিনিই ‘আদি শক্তি’, পরাপ্রকৃতি। যিনি সৃষ্টির উৎস এবং বিনাশের দায়িত্বও নিজে গ্রহণ করেন। এই ভয়ঙ্কর রূপেই তিনি পূজিতা, আর এখানেই সনাতন ধর্মের বৈচিত্র্য, যেখানে ভয়কেও ভক্তির আসনে বসানো হয়।
অথর্ববেদ থেকে মহাভারত, দেবী মাহাত্ম্যম থেকে কালিকা পুরাণ, প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে কালী এক বহুরূপিণী দেবী। কোথাও তিনি কালরাত্রি, কোথাও রক্তবীজ সংহারিণী, আবার কোথাও ষোড়শীর অন্তর্ভুক্ত পরাবিদ্যা। কালিকাপুরাণে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে ‘অধিষ্ঠাত্রী পরাপ্রকৃতি’ হিসেবে। কালী শুধু দেবী নন, তিনি ব্রহ্ম। তিনিই সর্বোচ্চ তত্ত্ব।
আরও পড়ুনঃ অবিশ্বাস্য! অলৌকিক! দীপান্বিতা আমাবস্যায় ভয়ংকর; একদিনের রুদ্রমূর্তি মায়ের!
কালীমূর্তির সবচেয়ে আলোচিত দিক হল, শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী। বেরিয়ে আছে জিভ। এই চিত্রটির তিনটি ব্যাখ্যা প্রচলিত।দার্শনিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক। দার্শনিক ব্যাখ্যা মতে, শক্তিহীন শিব মানে শব অর্থাৎ জড় পদার্থ মাত্র। কালী তাঁর উপর দাঁড়িয়ে যেন বোঝাচ্ছেন, শক্তি ছাড়া চৈতন্যও নীরস।
পৌরাণিক কাহিনিতে দেখা যায়, রক্তবীজ বধের সময় দেবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। তখন তাঁকে থামাতে শিব নিজেই তাঁর পথে শুয়ে পড়েন, আর দেবী নিজের পায়ে স্বামীকে পদদলিত করায় লজ্জায় জিভ কামড় দেন। এই চিত্রটিই আজকের দক্ষিণাকালী মূর্তির ভিত্তি।
কালীপুজোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৭ সালে কাশীনাথের ‘শ্যামাসপর্যায়বিধি’ গ্রন্থে। কিন্তু কালীপুজো বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ১৮ শতকের শেষ দিকে, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবর্তনে। এরপর তাঁর পৌত্র ঈশানচন্দ্র ও কলকাতার বাবুরা এই পুজোকে উৎসবের রূপ দেন। ক্রমে দুর্গাপুজোর পাশে দাঁড়িয়ে কালীপুজো হয়ে ওঠে বাংলার আরও এক অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। রামপ্রসাদের গান থেকে শুরু করে চণ্ডীদাসের পদ, লোকায়ত বিশ্বাস হয়ে কালী তখন শুধুই ভয়ঙ্কর নন, বাঙালির ঘরে ঘরে ‘মা’ হয়ে উঠেছেন।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগেই বাংলাদেশে কালীপুজোর প্রচলন থাকলেও, দীপাবলি বা দীপান্বিতা উৎসব তখনও বাংলায় বিস্তৃত হয়নি। পশ্চিম ভারতে দীপাবলি যেমন আলোর উৎসব, বাংলায় কালীপুজোর সঙ্গেও তা যুক্ত হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। বিশেষত কলকাতার বাবু সমাজের উৎসবপ্রিয়তা ও প্রতিযোগিতার সৌজন্যে।
আরও পড়ুনঃ হুগলির তারকেশ্বরের ‘ছেলে কালী’! খেলার ছলে শুরু পুজো পেরিয়েছে ১০০ বছর
ধনীরা তেল-প্রদীপে, পরে গ্যাস বাতিতে আলোর বাহার লাগাতেন। বাজির ঝলকে মধ্যরাত ভরে উঠত আতসবাজির রঙে। গান, পানসি, বাজি পোড়ানো আর কখনও পতিতাপল্লীতে বাবুদের প্রতিযোগিতা। সব মিলিয়ে ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে কালীপুজো হয়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক হইহইয়ের পর্ব।
কলকাতার আদি বারোয়ারি কালীপুজোর সূত্রপাত ১৮৫৮ সালে বিহারীলাল বসুর হাতে। শুরুতে এটি ছিল পরিবার-ঘনিষ্ঠ পুজো। কিন্তু ১৯২০-র দশকে তা হয়ে ওঠে ‘আদি বারোয়ারি কালীপুজো’।
এখানেও কাহিনি প্রবাহিত হয় মানুষ বলি থেকে কুমড়ো ও আখ বলিতে। মূর্তি বদলায় শ্মশানকালী থেকে দক্ষিণাকালীতে। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু হয় নাটক, কবিগান। সঙ্গে যুক্ত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা। ১৯৪৫ সালে এই পুজোর উদ্যোক্তারা আইএনএ রিলিফ ফান্ডে অনুদানও দেন।
১৯২৮ সাল থেকেই বাংলায় শুরু হয় সার্বজনীন কালীপুজোর চল। বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়। পটুয়াটোলা, হ্যারিসন রোড (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড), শিমলা ব্যায়াম সমিতি থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ সোসাইটির পুজো, সব মিলিয়ে কালীপুজো হয়ে সামাজিক সংহতিরও প্রতীক।
সব মিলিয়ে কালী কেবল পূজিত হন না, তিনি বাঙালির সাহিত্যে, গানে, জীবনবোধে ও প্রতিবাদেও জায়গা করে নিয়েছেন। শ্মশানে তাঁর পুজো, মধ্যরাত্রির ভয়াল রূপ, অথচ ঘরের কোণে মাটির মূর্তিতে শিশুর মতো স্নেহময়ী মায়ের দ্বৈত রূপই তাঁকে করে তোলে ব্যতিক্রমী।
বাঙালির কালীপুজো এক ঐতিহাসিক অভিযাত্রা। তন্ত্রের শ্মশান থেকে বাবুদের আঙিনা, আবার সেখান থেকে বারোয়ারি ঘুরে সর্বজনীন হয়ে ওঠা পর্যন্ত কালী শুধু দেবীই নন, বিস্ময় ও সংস্কৃতিও। যে কারণে ভয় আর প্রেমের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই ‘করালবদনা’ আজও বাঙালির আধ্যাত্মিক অভিভাবক।