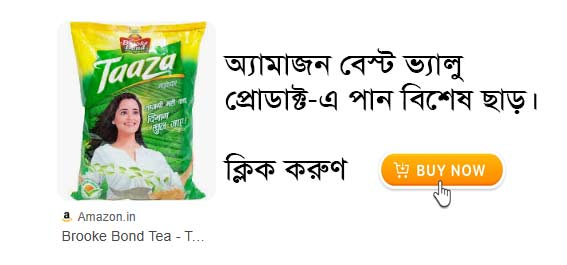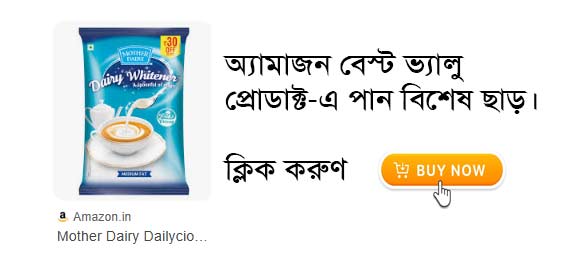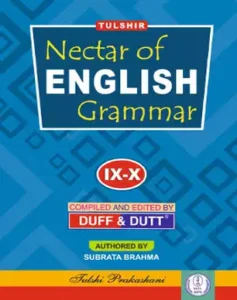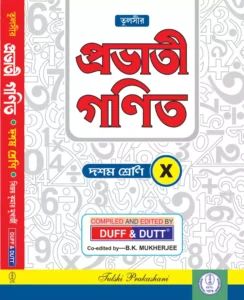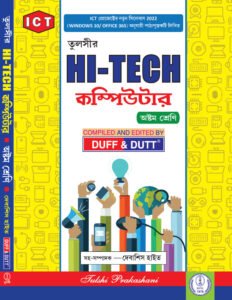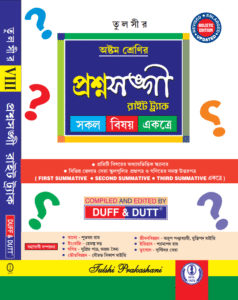কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়িঃ
অবিভক্ত জলপাইগুড়ির আর্থসামাজিক চরিত্র ছিল জোতদার-আধিয়ার ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চা বাগান স্থাপনের মূল কারিগর হয়ে উঠলে পুরোনো ওই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। চা শিল্পের জন্য যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ পুঁজি, ব্যবস্থাপক, এমনকি অদক্ষ শ্রমিক- সবকিছুই বাইরে থেকে আনা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের এতে কোনও ভূমিকা ছিল না। পুঁজিবাদী বাগিচা অর্থনীতির গোড়াপত্তনের পর ১৯০৯ সালে ডুয়ার্সের চা কোম্পানিগুলির ডিভিডেন্ড হয় ১৭ শতাংশ। ১৯১৫ সালে বেড়ে হয় ৪৭ শতাংশ।
প্রথম দিকে চা বাগান পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ডুয়ার্সে অন্য ইউরোপিয়ান মালিকানার চা কোম্পানিও ছিল। ওই সংস্থাগুলি ভারতে তাদের বিভিন্ন ফার্ম কিংবা ব্যক্তিগত উৎস থেকে টাকা সংগ্রহ করত। এলেনবাড়ি ও মানাবাড়ি বাগান দুটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলকাতার এক ব্যাংক ম্যানেজার, দার্জিলিংয়ের এক চা শিল্পপতি এবং ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংকের এক ডেপুটি ম্যানেজারের মাধ্যমে। পরে এসব বাগানের পরিচালনা শুরু হয় ডুয়ার্স ব্রাদার্স নামে। যা ছিল পুরোদস্তুর ব্রিটিশ এজেন্সি।
আরও পড়ুনঃ অবহেলায় “বাংলা”! দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী পুজোতে বাজলো না; ছট উপলক্ষে স্টেশনে স্টেশনে বাজছে গান
এসব চা শিল্পে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের খণ্ডিত কিছু উদাহরণ তো বটেই। ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা রাষ্ট্রীয় মদতে স্বজনপোষণের পুঁজিবাদ চা বাগানে সেইসময় থাকলেও এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ সময়কালে জলপাইগুড়ির দেশীয় চা শিল্পপতিরা ১১টি কোম্পানি তৈরি করে ফেলেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলায় তখন ৪৭টি বাগান স্বদেশি মালিকানাধীন ছিল। তাতে মোট লগ্নি ছিল ২ কোটি ৬৭ হাজার ৫৭৯ টাকা। এর মধ্যে ভারতীয়দের লগ্নি ছিল ৭৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা।
জলপাইগুড়ির আইনজীবী কিংবা অন্যান্য পেশার কিছু মানুষ চা বাগানে বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। তাঁদের অনেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে এসে চা বাগান গড়ে তোলায় এগিয়ে আসেন। প্রত্যেকে ছিলেন মধ্যবিত্ত। স্বভাবত তাঁদের কাছে প্রচুর টাকা ছিল না। তখনকার দিনে সব আর্থিক সংস্থা, ব্যাংক ছিল ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে। ভারতীয়রা শিল্প গড়তে চাইলে ওইসব সংস্থা থেকে অর্থসাহায্য পেতেন না।
বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ির শিল্পপতিরা টাকা জোগাড় শুরু করলেন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী কিংবা অবাঙালি মহাজনদের কাছ থেকে। টাকা সংগ্রহ করতে কিছু বাঙালি চা বাগান মালিক পরিবারের গয়নাগাটি বন্ধক রাখার এমনকি বিক্রি করার নজিরও ছিল। ওই মালিকরা পরে জলপাইগুড়ি ব্যাংকিং অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন গড়ে তোলেন। যার নাম পরে হয় বেঙ্গল ডুয়ার্স ব্যাংক।
সময়ের সঙ্গে ভারত ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশে চা শিল্প গড়ে ওঠে। ফলে ভারতের চায়ের আর বিশ্বে একচেটিয়া বাজার থাকেনি। অথচ উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকে। সংকট তৈরি হওয়ায় ইউরোপিয়ানরা বাগান বিক্রি করতে থাকেন। কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির ভারতীয়রাও আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলেন না। তাই জলপাইগুড়ির প্রায় ১০০টি বাগান হস্তান্তর হয়ে যায়।
কেনে কয়েকটি বাণিজ্যিক কোম্পানি। ১৯৯১ সালের উদারীকরণও ডুয়ার্সের চা শিল্পে বিদেশি পুঁজি আনতে পারেনি। বরং বাগান মালিকরা বেশি লাভের আশায় অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুরু করেন।
নানা কারণে বড় বাগানগুলি দিনে-দিনে রুগ্ন ও অলাভজনক হয়ে ওঠে। তাই বড় পুঁজির বিনিয়োগ আর নেই। ডানকান্স, উইলিয়ামসন্স মেগার-এর মতো কোম্পানির একসময় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল চা শিল্পে। তাঁরা এখান থেকে প্রচুর আয় করলেও সেই টাকা অন্যত্র বিনিয়োগ করতে থাকেন। সার, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পেও চায়ের পুঁজি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদাহরণও রয়েছে।
আরও পড়ুনঃ ফের বিনোদুনিয়ায় আছড়ে পড়ল দুঃসংবাদ; প্রয়াত সতীশ শাহ
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পে লগ্নি শুরু করেন বাগান মালিকদের একাংশ। ১৯৯১ সালের উদার অর্থনীতির সময়কালে ডানকান্স, উইলিয়ামসন্স মেগার-এর মতো কোম্পানিগুলি অধিক লাভের লক্ষ্যে বড় বাগানকে বঞ্চিত করে ইসলামপুর মহকুমায় নতুন চা বাগান তৈরি শুরু করে। এতে ধীরে ধীরে বড় বাগানগুলি আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নতুন লগ্নি না হওয়ায় এবং নতুন আবাদ তৈরি না করায় বাগানগুলির উৎপাদনশীলতা কমতে থাকে। পুরোনো চা গাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের পাতা উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
চা শিল্প এখন গভীর সংকটে। যাঁরা নতুন লগ্নি করছেন, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। তাঁরা মূলত ট্রেডার। বাগান পরিচালনার অভিজ্ঞতাও নেই। তাঁরা চটজলদি আয়ের ভাবনা নিয়েই বন্ধ কিংবা পরিত্যক্ত চা বাগানগুলির মালিকানা নিচ্ছেন। বর্তমান প্রজন্মও আর শ্রম নিবিড় চা বাগিচায় কায়িক পরিশ্রমে আগ্রহী নয়। আবার চাইলেই চা বাগানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাতা তোলা কিংবা অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না যন্ত্রের উপযুক্ত চা গাছের পরিসর না থাকায়। যা করতে কোটি কোটি টাকা লগ্নি প্রয়োজন। সেই বিনিয়োগে এগিয়ে আসারও কেউ নেই।
অবস্থা এমনই যে, উত্তরবঙ্গের ২৭৬টি চা বাগানে এ বছর রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দিলেও কোনও কোনও মালিক কিস্তিতে মিটিয়েছেন। অধিকাংশই বাজার থেকে ধার করে বোনাসের টাকা জোগাড় করেছেন। চা শিল্প যে আর লাভজনক নয়, তার বড় প্রমাণ গুডরিক-এর মতো বড় শিল্পগোষ্ঠীর চলতি বছরে ডুয়ার্সের দুটি বাগান বিক্রি করে দেওয়া।
এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের চা বাগান আর ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে নেই। অধিকাংশই কোনওভাবে অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন ও খরচের যে মডেল বড় চা বাগানে গত দেড়শো বছর ধরে চালু ছিল, ১৯৯১ সালের পরিবর্তিত শিল্পনীতির পর তা আর ক্ষুদ্র চা বাগান ও বটলিফ ফ্যাক্টরির মডেলের সঙ্গে পেরে উঠছে না। ডুয়ার্সে বাঙালি মালিকানাধীন বাগানগুলি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে একবার বড় রকমের হাত বদল হয়। এখন আরও কিছু হস্তান্তর শুরু হয়েছে। ফলে পুঁজিই যেখানে কার্যত ‘আইসিইউ’-তে, সেখানে ক্রোনি পুঁজির বিকশিত হওয়ার আর অবকাশ নেই।